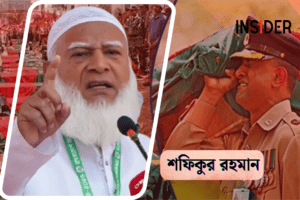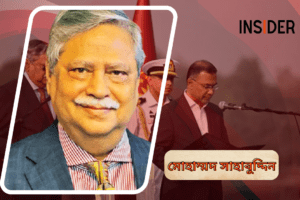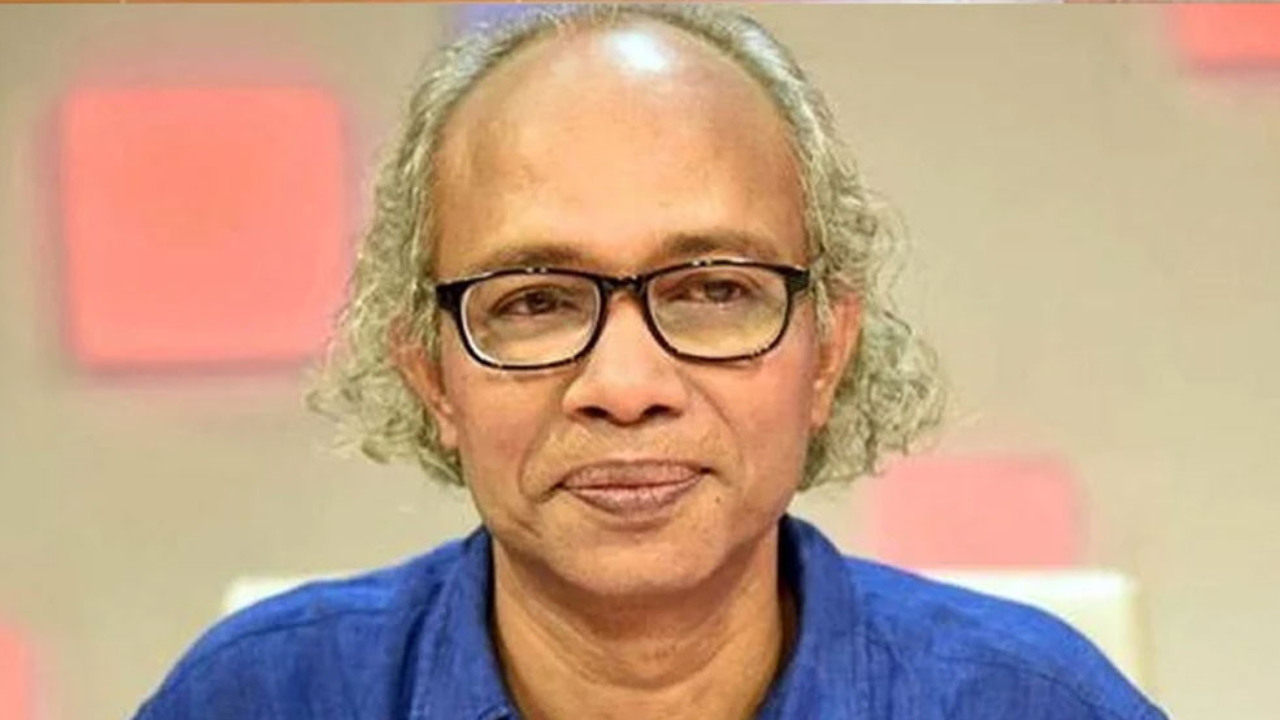সোয়েব মাহমুদ
মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমাদের মানসপটে সচরাচর যে চিত্রটি ভেসে ওঠে, তা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক—হাতে স্টেনগান উঁচিয়ে থাকা কোনো তরুণ কিংবা লুঙ্গি পরিহিত দামাল কৃষক। আমরা সগর্বে ‘ত্রিশ লাখ শহীদ’-এর কথা বলি, কিন্তু ‘দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম’-এর কথা উল্লেখ করি অনেকটা প্রথাগত বুলি আউড়ানোর মতো। ইতিহাসের প্রচলিত বয়ানে নারীর অবদানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল ‘ত্যাগ’ আর ‘নির্যাতন’-এর ফ্রেমে বন্দী রাখা হয়েছে। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, একটি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ যদি নারী হয় এবং তাঁরা যদি দীর্ঘ নয় মাস নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন, তবে স্বাধীনতা অর্জন ছিল সুদূর পরাহত। আজ ইতিহাসের ধুলো সরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও অবদান বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরি।
ইতিহাসের অন্ধবিন্দু ও নারীর ভূমিকা
প্রথাগত ইতিহাস ও গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে চিত্রায়ণ, সেখানে নারীদের ভূমিকা মূলত ‘সহায়ক’ বা ‘সেবিকা’ হিসেবেই সীমাবদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা বা আহতদের সেবা করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক সাপোর্ট। পাকিস্তানি বাহিনীর কড়া নজরদারির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ জোগানো ছিল মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে করা কাজ। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে নারীদের অবদানকে কেবল এই চৌহদ্দিতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছে। অথচ এর বাইরেও নারীরা ছিলেন সম্মুখ সমরের যোদ্ধা, গ্রেনেড চার্জকারী, দক্ষ গুপ্তচর এবং তুখোড় পরিকল্পনাকারী।
অস্ত্র হাতে রণাঙ্গন: প্রথা ভাঙার ইতিহাস
মুক্তিযুদ্ধে নারীরা কেবল পরোক্ষ সহায়তা দেননি, বরং অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরেও অংশ নিয়েছেন—এই সত্যটি মূলধারার ইতিহাসে প্রায়শই উপেক্ষিত। কলকাতার ‘গোবরা ক্যাম্প’-এ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় তিন শতাধিক নারী গেরিলা যুদ্ধের কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁরা কেবল নার্সিং নয়, শিখেছিলেন সিভিল ডিফেন্স ও অস্ত্র চালনা। আগরতলার লেম্বুছড়া ক্যাম্পেও নারীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।
পাবনার শিরিন বানু মিতিল পুরুষের পোশাক পরে, চুলে ছাঁট দিয়ে পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও পুলিশ লাইন দমনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহসী ভূমিকা প্রমাণ করে যে, দেশমাতৃকার মুক্তির প্রশ্নে নারীরা লিঙ্গ পরিচয় তুচ্ছ করতে প্রস্তুত ছিলেন। একইভাবে খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবি ছিলেন একাধারে গুপ্তচর ও সম্মুখযোদ্ধা। প্রায় নয়টি সম্মুখ সমরে অংশ নেওয়া এই বীর নারী শরীরে গুলি বহন করেছেন আমৃত্যু। ১১ নম্বর সেক্টরের তারামন বিবি কিংবা বরিশাল অঞ্চলের নারী কমান্ডার করুনা বেগম ও আলেয়া বেগমের নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলার ইতিহাস প্রমাণ করে—নারীরা ‘অবলা’ নয়, বরং তাঁরা ছিলেন রণাঙ্গনের ‘সাবলা’ ও দুঃসাহসী যোদ্ধা।
সেবা ও শুশ্রূষা: মৃত্যুর দুয়ারে পাহারাদার
যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে নারী চিকিৎসক ও সেবিকাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ত্রিপুরার বিশ্রামগঞ্জে বাঁশ ও ছন দিয়ে নির্মিত ৪৮০ শয্যার ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’ ছিল এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালের কমান্ডিং অফিসার (CO) ছিলেন ডা. সিতারা বেগম। যুদ্ধকালীন সময়ে কোনো সেক্টরের অধীনে একটি হাসপাতালের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব একজন নারীর কাঁধে থাকা নেতৃত্বের এক অসাধারণ উদাহরণ। অপর্যাপ্ত ওষুধ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব সত্ত্বেও সুলতানা কামাল, পদ্মা রহমান, লুলু বিলকিস বানু এবং শাহনাজ পারভীনের মতো নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় সেবা প্রদান করেছেন।
গোয়েন্দা তৎপরতা ও লজিস্টিকস: নীরব বিপ্লব
যুদ্ধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো সঠিক তথ্য বা ইন্টেলিজেন্স। এই ক্ষেত্রে নারীরা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বোরকার আড়ালে বা বাজারের থলিতে করে গ্রেনেড ও গুলি পাচার করা ছিল তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক সাহসিকতা। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়, অবরুদ্ধ ঢাকায় বসে কীভাবে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ‘সেফ হাউজ’ পরিচালনা করেছেন। রুমী-বদিদের মতো গেরিলা যোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ছিল এই মায়েদের আঁচল। পিরোজপুরের ভাগীরথী পাকিস্তানি ক্যাম্পে কাজ করার ছলে ম্যাপ ও গোপন তথ্য পাচার করতেন, যার করুণ পরিণতি হিসেবে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই আত্মত্যাগ কোনো অংশেই রণাঙ্গনের শহীদের চেয়ে কম নয়।
বীরাঙ্গনা: করুণার পাত্র নাকি যুদ্ধের বীর?
মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ওপর চালিত পৈশাচিকতাকে কেবল ‘ধর্ষণ’ বা ‘সম্ভ্রমহানি’ হিসেবে দেখা একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধর্ষণকে একটি ‘যুদ্ধাস্ত্র’ (Weapon of War) হিসেবে ব্যবহার করেছিল বাঙালির মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। সুতরাং, নির্যাতিত নারীরা যুদ্ধের ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’ নন, তাঁরা ছিলেন সরাসরি টার্গেট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নারীদের ‘বীরাঙ্গনা’ উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে তাঁরা প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ২০১৪ সালের হাইকোর্টের রায়ের পর সরকার ২০১৫ সালে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে গেজেটভুক্ত নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন, যা একটি ঐতিহাসিক দায়মোচনের সূচনা মাত্র।
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আগামীর দায়
নারীদের বিশাল অবদানের তুলনায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা খেতাবের পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক। খেতাবপ্রাপ্ত ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন মাত্র দুজন নারী—ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম এবং তারামন বিবি। কাঁকন বিবি কিংবা শিরিন বানু মিতিলের মতো অসংখ্য নারী, যারা গ্রেনেড ছুড়েছেন বা মাইন পুঁতেছেন, তাঁরা যথাযথ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বাইরেই রয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধরীতি অনুযায়ী, যারা লজিস্টিক সাপোর্ট বা গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন, তারাও ‘কমব্যাটেন্ট’ বা যোদ্ধা হিসেবে গণ্য হন। সেই হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের একটি বিশাল অংশই মুক্তিযোদ্ধা।
পরিশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল জেনারেল বা রাজনীতিবিদদের বয়ান নয়। এই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রতিটি গ্রামে, যেখানে নারীরা নিজেরা না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছেন, অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন এবং প্রয়োজনে নিজেরা অস্ত্র ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিনির্মাণে নারীদের কেবল ‘ভিকটিম’ হিসেবে না দেখে তাঁদের ‘যোদ্ধা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি। পাঠ্যপুস্তক ও জাতীয় মানসে তারামন বিবি বা সেতারা বেগমের পাশাপাশি নাম না জানা হাজারো নারীর অবদানকে সমুজ্জ্বল করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ, তাঁদের ইস্পাতকঠিন মনোবল ও ত্যাগ ছাড়া বাংলাদেশের মানচিত্র অর্জন অসম্ভব ছিল।